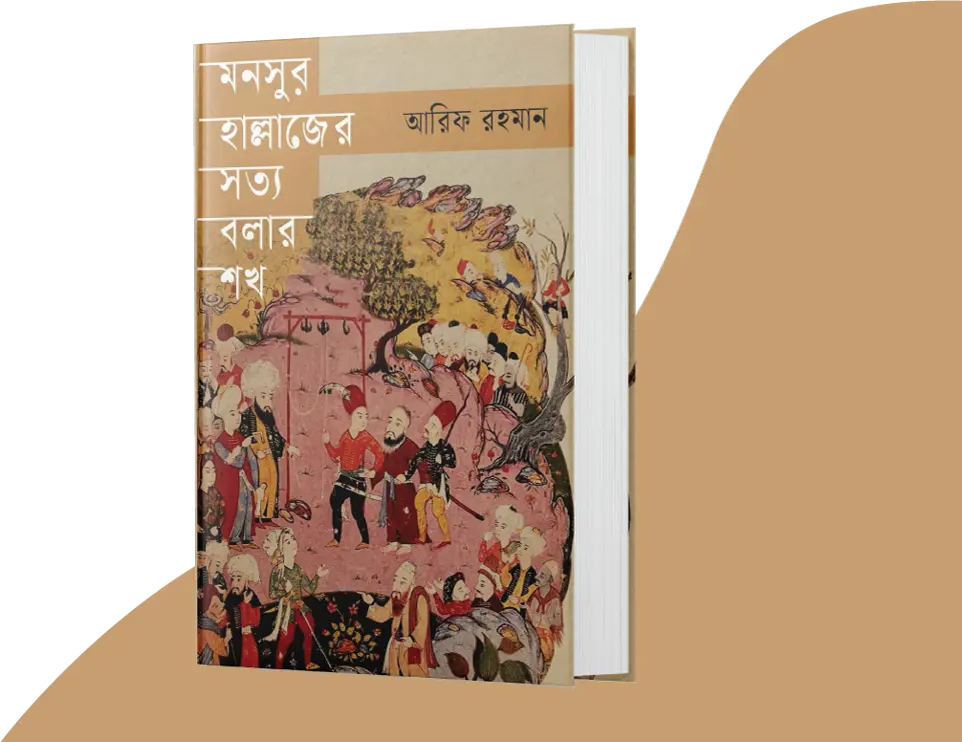কয়েক বছর আগে, খুব সকালে একদিন মাটি কাটা শ্রমিকদের সাথে আলাপ কালে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছিলাম। সেটা হলো শ্রমিকদের অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষদের কাছে স্বাধীনতার মানে আসলে কি। সে সময়ে একজন মাটিতে কোদাল বসাতে বসাতে, আইন সম্পর্কে আমাকে ছবক দিয়েছিলেন। আসলে বাংলাদেশের আইন কিভাবে কাজ করে। তিনি বলেছিলেন, আইন আসলে একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার। আপনার কাছে টাকা আছে তো আইন আপনার হাতে আছে। আপনার হাতে কোদাল আছে তো আইন আপনাকে এই কোদাল দিয়েই কোপায় মারবে। অর্থাৎ আইন কৃষক-শ্রমিকদের জন্য এক রকম আর বড়লোক শ্রেণির জন্য আরেকরকম। এইভাবেই তিনি স্বাধীনতাকেও ব্যাখ্যা করেছিলেন।
যদিও সেরকম কোন ব্যাখ্যা আমি আজ পর্যন্ত খুব বেশি একটা বুদ্ধিজীবী মহলে পাই নাই। তথাপি সহুল আহমদ লিখিত শ্বাস নেয়ার লড়াই পড়তে গিয়ে মনে হলো, আমার ভাবনা গুলো তার লেখার সূত্রধরে বলে নেয়া যেতে পারে। যদিও একটা বই বা লেখা অথবা চিন্তার রিভিউ লেখবার মতো যথেষ্ট সময় দিয়ে ওঠা হয় নাই এই বইয়ের ক্ষেত্রে। বলা যায় এটাকে প্রাথমিক নোট হিসেবেই দেখা ভালো হবে।এখানে আমি বইটি পড়বার সময়ে আমার ভিন্নমত সমূহ এবং প্রাথমিক কিছু নোকতাকেই হাজির করতে চাইবো, যা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক এক্টিভিজম এর মধ্য দিয়ে পাওয়া আমার অভিজ্ঞতার সমষ্টি বলা যেতে পারে। এছাড়া তার লেখার অনেকাংশের সাথেই আমি একমত। সেসব বিষয়ে কথা বলবার মত ফুরসত এই মুহূর্তে নেই। সেজন্য সেসব ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলাম। বইটিতে রয়েছে ভূমিকা এবং মোট বারোটি লেখা ও একটি পরিশিষ্ট।
প্রথমেই বলে নেয়া দরকার যে, লেখক আসলে ভূমিকাতেই অনেক কথা বলেছেন। বলা যায় তার লেখা ভূমিকা এই গ্রন্থের অন্যতম দিক। সেক্ষেত্রে ভূমিকাটিও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবেই হাজির থেকেছে। ভূমিকাতেই লেখকের বর্তমান সময়ের অন্যতম কনসার্নের দিকগুলো পাওয়া যাবে। তাই ভূমিকার উপরে দু এক কথা বলতেই হচ্ছে। লেখক ভূমিকার শুরুতেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন করোনাকালে কিভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণি অবস্থান পরিষ্কার ভাবে উলঙ্গ হয়েছে। করোনাকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যে বৃহৎ পুঁজিপতি, গ্রামীণ মহাজন-জোতদার সামন্তশ্রেণি এবং আমলাদের রাষ্ট্র তা প্রকাশিত হয়েছে। একইসাথে এখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন যে সাম্রাজ্যবাদী প্রেসক্রিপশন নির্ভর তাও উঠে এসেছে।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র কী একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হিসেবেই জন্মলাভ করেছে?
লেখক ভূমিকায় ফ্যাসিবাদকে তিনি কিভাবে বুঝেছেন তা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গত শতাব্দীর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত ধারনার বাইরে এসে নতুনভাবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি চারটি বিষয়কে ফ্যাসিবাদের নির্দেশক হিসেবে দেখিয়েছেন, যেগুলো হলো, ঔপনিবেশিক আইন, সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং নয়াউদারনীতিবাদ।
এক্ষেত্রে লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ তিনি পুরানো ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা দ্বারা ফ্যাসিবাদকে বোঝার যে বিপদ তা থেকে বের হতে পেরেছেন। কারণ গত বারো বছরে, বাম পরিমণ্ডলে হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে,ফ্যাসিবাদ বলা হবে কিনা এটা নিয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিমিত্রভ লিখিত ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত থিসিস নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মতামত চালু আছে। তারা এর মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদকে দেখতে গিয়ে ভুলে যান যে, পৃথিবী এবং বিশ্ব গত শতাব্দী থেকে বদলে গেছে নানান ভাবেই। ফ্যাসিবাদকে তাই নতুনভাবেই সংজ্ঞায়িত করবার প্রয়োজন হাজির হয়েছে। যেক্ষেত্রে সহুল আহমদ কিছুটা বিন্দু ভাঙতে চেয়েছেন।
তিনি ফ্যাসিবাদের যে চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি বাদে বাকি তিনটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই ক্রিয়াশীল রয়েছে। তিনি যেহেতু এই তিনটিকেই ফ্যাসিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলছেন, সেহেতু প্রশ্ন আসে, তাহলে কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর লেখক দেন নি।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ১৯৭২ সালেই, তার গঠনের সময়েই, ঔপনিবেশিক আইনকে ভিত্তি করেছে। অর্থাৎ এই হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে এক ফ্যাসিস্ট প্রবণতাকে সঙ্গী করেই।১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাস্তবে বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে উল্টোমুখি প্রবণতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের ৭২ এর সংবিধান থেকেই শুরু করতে হবে। ৭২ এর সংবিধান নিজেই এক ফ্যাসিস্ট প্রবণতা যুক্ত সংবিধান। এই সংবিধান বাংলাদেশের বাঙালী ভিন্ন অন্য জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং উগ্র বাঙালি জাতিবাদি প্রবণতাকে আত্তীকরণ করেছে। শুধুমাত্র এই একটি উদাহরণ দিয়েই সংবিধানের স্বৈরতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র ৭২ এই শুরু হয়েছে।
বাঙালী জাতীয়তাবাদ নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যতম খুঁটি হিসেবে কাজ করেছে। ৭২ সালেই সাংবিধানিকভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে এই রাষ্ট্রের পরিচালনার মতাদর্শিক ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
এর সাথে লেখক নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিকে যুক্ত করেছেন। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি মূলত নব্বই এর দশক অথবা আশির দশক থেকে আলোচিত হচ্ছে। তবে নয়া উদারতাবাদ নব্বই দশক থেকেই ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমান আকার নিয়েছে। এই অর্থে বাকি তিন বৈশিষ্ট্যের বাইরে কেবল এইটাই নতুন একটা বিষয়। যা মূলত অর্থনীতি কেন্দ্রিক ধারনাকে নির্দেশ করে। সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধিত সংকট নয়া উদারনীতিবাদের নতুন মোড়কে হাজির হয়েছে। আজকের দিনে যে কোন সচেতন মানুষকেই নয়া উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে। নতুবা সে নিজেই এর খপ্পরে পড়বে। এমনকি আজকের দিনে যারা নয়া উদারনীতিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সেইসমস্ত বুদ্ধিজীবীরাও কোন না কোনভাবে এই নয়া উদারনীতিবাদের খপ্পর থেকে ব্যক্তিগত জীবনে বের হইতে পারেন না। সুতরাং এটাকে গুরুত্বের সাথেই পর্যালোচনা করা জরুরী।
উপরেই প্রশ্ন করেছিলাম যে, লেখক উদ্ধৃত তিনটি বৈশিষ্ট্যই যদি এই রাষ্ট্রের সূচনা থেকে থেকে থাকে, তাহলে কি আমরা বলবো যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হিসেবেই জন্মলাভ করেছে? যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের আরো একটু গভীর ভাবে ফ্যাসিবাদকে বুঝতে হবে। এবং এটাও পরিষ্কার করতে হবে যে অতীতের সাথে বর্তমানের কি কি পার্থক্য আছে, নাকি আদৌ কোন পার্থক্য নেই। আশা করবো লেখক এদিকে মনোযোগ দেবেন।
প্রাথমিকভাবে বলা যায় বাংলাদেশের অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে আজকের ফ্যাসিবাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ৭২ সালের রাষ্ট্র আজকের মত এতটা শক্তিশালী দানব হিসেবে হাজির হইতে পারে নাই। তার কলকব্জাগুলোও এরকম দানবীয় কামড় বসাইতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের আজকের সময়কে পার্থক্য করতে হবে এবং অতীতের ধারাবাহিকতাকেও ব্যাখ্যা করতে হবে।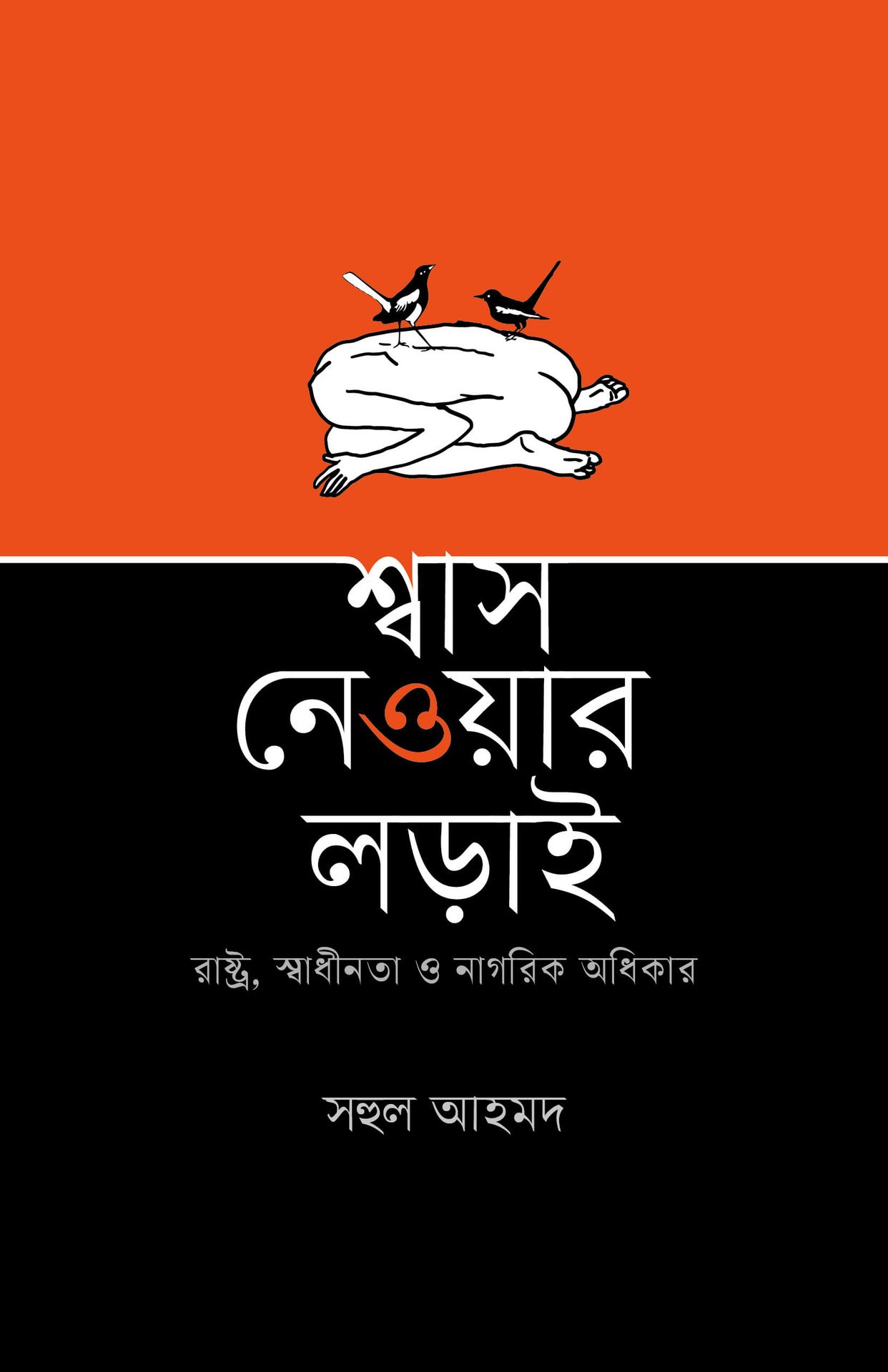
শ্বাস নেওয়ার লড়াই
লেখক: সহুল আহমেদ
মুদ্রণ মূল্য: ৪০০ টাকা
বাম পপুলিস্ট রাজনীতির বিপদ
এছাড়াও ভূমিকাতে তিনি শেষ পর্যায়ে এসে, বাম পপুলিস্ট রাজনীতির নতুন ধারার কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, প্রলেতারিয়েত বনাম বুর্জোয়া এই বৈপরীত্য দিয়ে আর সংগ্রামকে বোঝা যাবে না। তিনি বলছেন ডানপন্থী পরিচয়বাদী রাজনীতির বিপরীতে ‘নাগরিক’ পরিচয়কে মুখ্য করে তুলতে হবে। লেখকের এই বক্তব্যের সাথে একমত নই। তিনি যেভাবে পরিচয়ের রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত বনাম বুর্জোয়া বৈপরীত্য দিয়ে সংগ্রামকে বোঝা যাবে না তা সঠিক নয়। বরং বিপরীতভাবে বলা যায়, প্রলেতারিয়েত বনাম বুর্জোয়ার মধ্যেকার সংগ্রাম এখন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে।
জলবায়ু সমস্যা কারা সৃষ্টি করছে? পরিবেশকে উন্নয়ন নামে সহ বিভিন্নভাবে কারা ধ্বংস করছে? পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার মোড়লরাই তা করছে। এমনকি এলজিবিটিকিউ+ দের প্রশ্নও সামনে আসছে বর্তমানে। লেখক এই উদাহরণও দিতে পারতেন। পুরাতন সমাজতান্ত্রিক ধারনায় এটাকে ব্যাপকভাবে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। সোভিয়েত আমলে এমনকি চীনেও। কিন্তু আমরা দেখবো এসব কিছুকে “ক্লাসিক্যাল/র্যাডিকেল” মার্ক্সবাদী ধারাও নিজেদের সংগ্রামে আত্তীকরণ করছেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত গেরিলা পার্টি, ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট পার্টি ফিলিপাইনে ব্যাপকভাবেই জনপ্রিয়। তারা নিজেদের মধ্যেই ঘাঁটি অঞ্চলে সমকামী বিবাহকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছেন। তারা পরিবেশ রক্ষা বড় বড় আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন।তারা বলছেন, পরিবেশ এবং জলবায়ু সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই শ্রেণি সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমনকি ভারতের বস্তার সহ বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় মাওবাদীদের সংগ্রামের অন্যতম স্লোগান জল,জঙ্গল,জমিন রক্ষার লড়াই এগিয়ে নিন। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি বাম পপুলিস্ট রাজনীতি বাস্তবে নতুন বিপদই ডেকে আনবে। এটা নতুন কিছু দিতে সক্ষম হবে না। কারণ পপুলিস্ট রাজনীতি সেটা বাম নামে হোক আর ডান বা কম্যুনিস্ট, রূপগত কারণেই এটা রুট বিচ্ছিন্ন হবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছু ব্যক্তির আন্দোলন নৈতিকভাবে পরাজিত হবে। ব্যাপকভাবে পারসোনালিটি কাল্ট তৈরিরও সম্ভাবনা থাকবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে আমরা পপুলিস্ট বাম ধারার রাজনীতিকে দেখেছি কিছুটা। এর একটা বড় উদাহরণ, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আন্দোলন। সুতরাং আমার মতে এই প্রশ্নে লেখক বাস্তবে উত্তরাধুনিক প্রবণতাকেই আশ্রয় করেছেন। এর সাথে যুক্ত হবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ভাবে একে না দেখে বাইরে থেকে দেখা।বর্তমানে কমিউনিস্ট আন্দোলনেই ভেতর থেকে এইসব বিষয়কে নিয়ে বেশ কিছু পর্যালোচনা আছে। ভবিষ্যতে কখনো সে বিষয়ে বিস্তারিত লিখবো।
নিরঙ্কুশ বাকস্বাধীনতাও কি শ্রেণি নিরপেক্ষ?
আমাদের দেশে বর্তমান ফ্যাসিস্ট জমানায় আমরা সকলেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার দাবিতে লড়ছি। এক্ষেত্রে সহুল আহমদের সাথে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছি। তবে আমাদের সাথে তাদের বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বোঝা পড়ায় কিছু পার্থক্য চোখে পরছে। তার “বাক-স্বাধীনতার ফজিলত ও বাংলাদেশের হালচাল” লেখায় তিনি চমৎকার ভাবেই মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। যা বেশ তথ্য এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ। কিন্তু তার সাথে আমি কিছু বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করতে চাই।
আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ-প্রকাশনার স্বাধীনতা দাবি করছি। কিন্তু এই স্বাধীনতা কিভাবে আমরা প্রতিষ্ঠা করবো আমার আলোচ্য বিষয় সেখানেই। সহুল আহমদ একদিক থেকে এই আলাপের অবতারণা করেছেন। আমি একটু ভিন্নভাবে শুরু করতে চাই।
ধরুন সাংবিধানিকভাবে যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় এবং বাস্তবেই মত প্রকাশ কে বাধা না দেয়া হয় তাহলে কি নাগরিকের সার্বজনীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব? কারণ আমরা ইউরোপের এবং তথাকথিত সর্বোচ্চ উন্নত গণতন্ত্রের ইতিহাসটা জানি। যদিও আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী-নেতারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে ইউরোপে নেই তা টেনে আনেন। তারা এটা করেন, কারণ ইউরোপকে অথবা আমেরিকা-ব্রিটেনের গণতন্ত্র এখানে মডেল ছিলো, শাসকশ্রেণির কাছে এখনো এটাই বলা হয়। তবে সর্বোচ্চ “গণতান্ত্রিক” দেশেও কি সার্বজনীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব? যদি রাষ্ট্র কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ না ও করে?
ধরুন আমাদের দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সমস্ত কালাকানুন বাতিল করা হলো এবং তুলনামূলক নাগরিক গণতন্ত্র কায়েম হলো তাহলেই কি স্বাধীনতা মিলবে?
‘বইয়ের ‘ক্রসফায়ারের আইনি ভিত্তি’ শীর্ষক লেখায় খুব ভালোভাবে এসেছে যে, এই রাষ্ট্রের আইন বাস্তবে আইনীভাবেই ক্রসফায়ারের বৈধতা দেয়। আমরা যেটাকে ৭২ সাল থেকেই বলছি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড। এটাকে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলবার কোন সুযোগ নেই। একইসাথে এই লেখায় এদেশের তথাকথিত নামীদামী বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতাকেও প্রকাশ করেছেন লেখকদ্বয় (সহুল আহমদ ও সারোয়ার তুষার)। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে তথ্য-উপাত্তসহ ক্রসফায়ারের আইনি ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করা এবং তার সাথে বাস্তব উদাহরণকে মিলিয়ে নেয়ার পদ্ধতিতে এই লেখা পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে ক্রসফায়ার কিভাবে এই রাষ্ট্র টিকে থাকার হাতিয়ার হয়ে আছে। লেখকদ্বয়কে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে শুধুমাত্র এই লেখার জন্যেই।এরকম লেখা খুবই আছে এদেশের প্রেক্ষিতে।”
মত প্রকাশের স্বাধীনতা
আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে বলছি, সমস্ত দিক থেকে বাধাহীন হতে হবে সেইরকম স্বাধীনতা আমরা চাই। তথাপি এই স্বাধীনতার মধ্যেও রয়েছে শ্রেণি চরিত্র। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের দিয়ে শুরু করি। গার্মেন্টস শ্রমিকরা এদেশে ওভারটাইম মিলিয়ে কেউ কেউ ১৪ ঘণ্টা অব্ধি কাজ করেন। এরপরে আছে তার সাংসারিকসহ অন্যান্য কাজ। যে এক দুদিন ছুটি তারা পায় সেই সময়টাও তাদের ঘরের কাজ করতে হয় অথবা একটু আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতে কেটে যায়। গার্মেন্টস নারী কর্মীরা তো এক্ষেত্রে দম ফেলার সময়ও পান না। এক্ষেত্রে যদি চিন্তার সর্বোচ্চ স্বাধীনতাও দেয়া হয়, তার কি তা করা সম্ভব? তার কাজের এই পরিস্থিতি বজায় রেখে। এই কারণেই ইউরোপের কথাও বলছিলাম শুরুতে। সেখানেও সার্বজনীন স্বাধীনতা নেই। কারণ সেখানেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা। তবে সেই স্বাধীনতা বুর্জোয়া অর্থে আমাদের দেশের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। তবুও সেখানে শ্রমজীবীদের নিরঙ্কুশ কোন স্বাধীনতা নেই। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমনভাবে শ্রমিকদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে যে তাদের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করবার বাস্তবতা টুকুই থাকে না।
আমরা গার্মেন্টস শ্রমিকদের কথা বলছিলাম, তো এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা যদি চিন্তা করার সময়ই না পান তাহলে কিভাবে তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবেন? আমাদের এই প্রশ্নকে অতি অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। এইদিকে লেখক দিক নির্দেশ করতে পারেন নাই। তিনি বুর্জোয়া নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারটা চমৎকার ভাবে এনেছেন। কিন্তু মত প্রকাশের ও চিন্তার স্বাধীনতার শ্রেণি প্রকৃতি আনতে পারেন নি।
সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও প্রকাশ-প্রচার ও প্রকাশনার স্বাধীনতা
লেখক তার লেখার ভূমিকায় সংবাদ পত্রের কর্পোরেট মালিকানা এবং রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ততাকে ভালোভাবেই এনেছেন। তবে এর সাথে যুক্ত করে আমি বলতে চাই যে, সংবাদ পত্র প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতের সাথে সাথে এটা শ্রমজীবী শ্রেণি কিভাবে ভোগ করতে পারে সেটা বলেন নাই। দেখেন, এদেশের কৃষকদের ও শ্রমিকদের কি দুর্বিষহ পরিস্থিতি। তারা ভাত-মাছ-মাংসের স্বাধীনতা দাবি করছেন। আমি কোনভাবেই এই দুটোকে মুখোমুখি দাড় করাতে চাচ্ছি না। দুটোকে মিলিতভাবে দেখতে চাইছি। আজকের দিনে একটা সাধারণ মানের পত্রিকা চালু করতে হলেও যে অর্থনৈতিক যোগান দরকার হয় সেটা কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কাগজের দামের দিকে লক্ষ্য করুন। ২৮০ পৃষ্ঠার বই এর মুদ্রিত মূল্যও ৪০০ টাকা। শ্রমজীবীদের পক্ষে এই ধরনের উদ্যোগ সার্বজনীনভাবে কি সম্ভব? সম্ভব নয়। সুতরাং সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতাকে অবশ্যই এই শ্রেণির স্বাধীনতার প্রশ্নকে পরিষ্কারভাবে যুক্ত করে আলোচনা করতে হবে। নতুবা তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সার্বিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হবে।
মিছিল সমাবেশ ও সভা করার স্বাধীনতা
আমি শেষ ২০১৮ সালেও ঢাকা শহরে এমনকি মহানগর শহর ও উপজেলা শহরের সভা-সেমিনার করবার হলগুলোর ভাড়াকে হিসেব করে দেখেছি, ন্যূনতম ২০০০ হাজার টাকার নিচে নিম্নমানের হলরুম পাওয়াও সম্ভব নয় হাফ বেলার জন্যেও।শ্রমজীবী জনগণ নিজ উদ্যোগে মাসে একদিন সভা করতে চাইলেও তাদের অন্তত হাফ বেলার টাকা খরচ করতে হবে। এটা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব?
এমনকি উন্নয়নের নামে সভা-সমাবেশ করবার জায়গাগুলোকেও সংকুচিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মহানগর নাট্যমঞ্চ এবং শাহবাগে মেট্রোরেল, প্রেসক্লাবে মেট্রোরেল। এসব জায়গায় শ্রমজীবী জনগণ সহজে আসতেও পারেন না। যদি সভায় পুলিশ বাধা নাও দেয়।
অন্যদিকে উপরের আলোচনায় বলেছি শ্রমজীবী জনগণের জীবনের সময়কে কিভাবে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ সভা করবার স্বাধীনতা পেলেও অফিসে ছুটির ব্যবস্থা না থাকলে এটা এই ব্যবস্থাতেও সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাবেশ করবার স্বাধীনতা চাইবার সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণ কিভাবে সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে সেটাও আমাদের বলতে হবে। নতুবা এই স্বাধীনতা মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত নাগরিকের স্বাধীনতা হিসেবে থেকে যাবে।
আমাদের এজন্য শ্রমজীবী অঞ্চলে অবাধ সভা করবার জন্য হলরুম, মুক্তাঙ্গন, অফিস ছুটি এমনকি শিল্প কারখানায় শ্রমিকরা মিলে পত্রিকা বের করতে চাইলে তাদের পত্রিকা প্রকাশের অর্থের ব্যবস্থার কথাও বলতে হবে।
যদিও উপরিউক্ত দাবিগুলো এই রাষ্ট্র এমনকি সর্বোচ্চ তথাকথিত গণতন্ত্রেও দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য একদিকে আমাদের এই দাবিসমূহ শ্রমজীবীদের মধ্যে জনপ্রিয় করতে হবে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রকে পাল্টাবার আমূল সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে।
ক্রসফায়ার, আইন ও সম্মতি
বইয়ের ‘ক্রসফায়ারের আইনি ভিত্তি’ শীর্ষক লেখায় খুব ভালোভাবে এসেছে যে, এই রাষ্ট্রের আইন বাস্তবে আইনীভাবেই ক্রসফায়ারের বৈধতা দেয়। আমরা যেটাকে ৭২ সাল থেকেই বলছি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড। এটাকে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলবার কোন সুযোগ নেই। একইসাথে এই লেখায় এদেশের তথাকথিত নামীদামী বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতাকেও প্রকাশ করেছেন লেখকদ্বয়। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে তথ্য-উপাত্তসহ ক্রসফায়ারের আইনি ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করা এবং তার সাথে বাস্তব উদাহরণকে মিলিয়ে নেয়ার পদ্ধতিতে এই লেখা পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে ক্রসফায়ার কিভাবে এই রাষ্ট্র টিকে থাকার হাতিয়ার হয়ে আছে। লেখকদ্বয়কে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে শুধুমাত্র এই লেখার জন্যেই।এরকম লেখা খুব কমই আছে এদেশের প্রেক্ষিতে।
ক্রসফায়ার নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ “ক্রসফায়ার : সম্মতি, ভয় ও রাজনীতি”-তে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা চোখে পড়ে। কিভাবে এই রাষ্ট্র ক্রসফায়ার এর মাধ্যমে নিজেদের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখে। একইসাথে কোন শ্রেণি ক্ষমতায় আছে আর কোন শ্রেণি প্রধানত ক্রসফায়ার এর শিকার সেটাও জানা যাচ্ছে লেখাটির মাধ্যমে। রাষ্ট্র কিভাবে ক্রসফায়ার এর সম্মতি উৎপাদন করে? কেন জনগণের এক বিরাট অংশ ক্রসফায়ারের পক্ষে মতামত দেন সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক সহুল আহমদ। তিনি দেখিয়েছেন এই যে জনগণের ক্রসফায়ারের পক্ষে কথা বলার আর শাসকদের ক্রসফায়ারের পক্ষে ওকালতির মধ্যে পার্থক্য আছে। জনগণের এই পক্ষে দাঁড়ানোকে তিনি বলছেন রাষ্ট্রের বিচারহীনতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। আসলে আদৌ এই রাষ্ট্র কি বিচারহীনতা তৈরি করেছে নাকি এই রাষ্ট্র আসল অপরাধীদের বিচার করতেই পারে না? এই উত্তর আমি লেখকের লেখায় পাইনি। আশা করি লেখক এই দিকটাও ভাববেন। এখানে দেখা যাবে কিভাবে ক্রসফায়ার বর্তমানে বাণিজ্যেও পরিণত হয়েছে। শত শত কোটি টাকার ক্রসফায়ার বাণিজ্য তৈরি হয়েছে। এটা এখন বিরাট লাভ জনক ব্যবসা।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ক্রসফায়ার শুরু হয়েছে তার সূচনালগ্ন থেকেই। প্রথমে এটা শুরু হয়েছে বিরোধী শ্রেণি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের হত্যা করবার মধ্যে দিয়ে। যেটা আস্তে আস্তে এক শ্রেণি কর্তৃক আরেক শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার পদ্ধতি। আমরা দেখবো যে, মাদক বিরোধী অভিযান মূলত দরিদ্র শ্রেণির বিরুদ্ধে শাসক ধনিক শ্রেণির শ্রেণি যুদ্ধ। রাষ্ট্র নানাভাবে এই কাজটি করছে। কিন্তু এই সময়ে ক্রসফায়ার এক অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে এইটা যে শ্রেণিযুদ্ধ তা ৭২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে এসেছে। কিন্তু বর্তমান ফ্যাসিবাদ যেহেতু তার নিজের শ্রেণির মধ্যেকার বিরোধী অংশকেও ছাড় দেয় না, সেহেতু তারা এখন নিজেদের শ্রেণির বিরোধীদেরও ক্রসফায়ার দিয়েই দমন করতে চাইছে।
এই কারণেই দেখা যাবে যে, বিএনপি বা শাসকশ্রেণির বিরোধী দলসমূহ শুধুমাত্র নিজেদের কর্মীদের ক্রসফায়ারের বিরোধিতা করেন। এরা বাস্তবে দরিদ্র শ্রেণি এবং তাদের পক্ষের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা করবার ব্যাপারে একাট্টা। সুতরাং ক্রসফায়ারকে শ্রেণি যুদ্ধ হিসেবেই দেখতে হবে আমাদের।
গণতন্ত্র কি সর্বোচ্চ উন্নত ব্যবস্থা?
“গণতন্ত্র ‘নিখোঁজ’, নাকি আদৌ ছিল না? অথবা ‘আমি জানি না’” প্রবন্ধটি মূলত আলী রিয়াজের নিখোঁজ গণতন্ত্র বই এর রিভিউ বলা চলে। এখানে লেখক নিজস্ব কিছু নোকতাও দিয়েছেন। এই লেখার সাথে আমি ভিন্নমত করি বলার চেয়ে বলা ভালো আমি গণতন্ত্রকে কোনো সর্বোচ্চ ভালো ব্যবস্থা মনে করি না। লেখায় একভাবে গণতন্ত্রকেই সর্বোচ্চ রূপ বিবেচনা করে আলোচনা করা হয়েছে। আমি মনে করি গণতন্ত্র বৈশ্বিক ব্যবস্থা হিসেবেই অকার্যকর হয়ে পরেছে। এটা দিয়ে আর বিশ্বের অগ্রগতি সম্ভব নয়। গত পঞ্চাশ বছরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে যা হয়েছে তা হলো, পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। ডিজিটাইলাইজড এর নামে সারা বিশ্বের মানুষকে নব্য দাসে পরিণত করা হয়েছে। মানুষের সমস্ত কিছুকে আধুনিক করার নামে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে লঙ্ঘনের মহোৎসব করা হয়েছে। আমেরিকা সহ সাম্রাজ্যবাদ পুরো বিশ্বকেই গণতন্ত্রের দোহায় দিয়ে লুটপাটের রাজত্বকে শক্তিশালী করেছে।গণতন্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে মূলত চূড়ান্ত মাত্রার ব্যর্থ একটা ব্যবস্থা। এখানে একটা নোকতাও দিয়ে রাখা দরকার। মতামত আদান প্রদান এবং মানুষের স্বাধীনতার পদ্ধতি হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ প্রাচীন কালেও ছিলো এমনকি এখনো রয়েছে। আমাদের পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার চর্চা এবং ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের পার্থক্যকে বুঝতে হবে।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কী দিয়ে সম্ভব? পুরানো ধাঁচের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রিপিটেশনও এখানে আর চলবে না। বরং বলা ভাল গণতন্ত্র ব্যর্থ। সমাজতন্ত্র গত শতাব্দীতে পরাজিত হয়েছে। তবুও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে নতুন ধরনের ব্যবস্থাই আমাদের খুঁজতে হবে। নতুবা আমরা এই গণতন্ত্রের ভুয়া খপ্পর থেকে বের হতে পারবো না।
অহিংস আন্দোলন- আন্দোলনের রূপ নিপীড়িতের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না
“নাগরিক আন্দোলন : কিছু সমসাময়িক পর্যালোচনা” নামক প্রবন্ধে লেখক, আন্দোলন এর রূপ হিসেবে অহিংস পন্থাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে আরেকজন লেখক জিন শার্প এর লেখা ও চিন্তাকে প্রসঙ্গ ধরে এগিয়েছেন। তিনি এখানে একটা জায়গায় গান্ধীর প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। জিন শার্প অহিংস আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হিসেবে গান্ধীকে ব্যাখ্যা করেন। অথচ গান্ধী নিজেই কত দ্বিচারিতা করেছেন তা সচেতন ইতিহাস পাঠক মাত্রই ধরতে পারবেন। অহিংস আন্দোলনের নেতা গান্ধী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনগণের সহিংস ক্ষোভকে কিভাবে মোকাবেলা করেছেন তা আমরা জানি। জিন শার্প এবং লেখকের মতামত অনুযায়ী অহিংস আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই গত পঞ্চাশ বছরের অধিককাল যাবত নাকি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু লেখার মধ্যে কোথাও কি সেইসব ফল তা আমরা জানতে পারিনি। আশা করি লেখক সেসব ভবিষ্যতে বলবেন অন্য কোথাও।
যেকোনো আন্দোলনে/সংগ্রামে মূলত পরস্পর বিপরীত দুই শক্তির লড়াই হয়। এক্ষেত্রে আন্দোলনের রূপ কোন এক পক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রধানত নির্ভর করে নিপীড়িত যার বিরুদ্ধে লড়ছে তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে/কিরকম হয় তার উপর। এটা কোনভাবেই শুধুমাত্র নিপীড়িতের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীতে ইতিহাসের সমগ্র পর্যায় জুড়ে সহিংস রক্তাক্ত পথই শাসককে গদি থেকে নামিয়েছে এবং নতুন কিছুর সূচনা করেছে। তবে কি নিপীড়িতরা সর্বদায় সহিংস হবে? এটা সোজাসাপ্টা উত্তর হলো না। বর্তমানে আন্দোলনের প্রধান রূপ হিসেবে যারা সহিংসতাকে বিচার করেন তারা কী স্বভাবজাতভাবেই সহিংস হোন? বাস্তবে কিন্তু এটা সত্য নয়। বরং দেখা গেছে নিপীড়িতের পক্ষে সর্বোচ্চ সহিংস রূপে সংগ্রামরত জনগণ বা তাদের নেতারা নিজেদের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার নমনীয় থাকেন। কিন্তু সবাই এটা সর্বদা থাকেন এমন নয়। দেখা গেছে আন্দোলনের সফলতার পরে অনেক নেতা ও সমাজ উলটো পথে হাটে। এটা লেখক তার লেখায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর মানে কি এই যে সহিংসতা আন্দোলনের রূপ হতে পারে না? উপরেই সহিংসতা কেন আন্দোলনের রূপ তা ব্যাখ্যা করেছি। এটা যে আন্দোলনকারীর উপর নির্ভর করে না তাও বলেছি। কিন্তু এটা ঠিক যে, লেখকের এই পর্যালোচনাকে আমলে নিতে হবে যে, কেন এবং কিভাবে পরবর্তীতে আন্দোলনের নেতা/কর্মীরা স্বৈরাচারও হয়ে ওঠেন। এজন্য আমরা নিজেদের মধ্যেকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির চর্চার পর্যালোচনায় কেবল করতে পারি। পুরো সহিংস পথকে বাদ দিয়ে নয়।
লেখক “অপরায়ন এর রাজনীতি” নামক প্রবন্ধে ভালোভাবেই পরিচয়বাদী রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তার এই লেখায় বোঝা যায় পরিচয়ের রাজনীতি কিভাবে শাসকদের সেবা করে এবং নিজেই এক দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা শেষ পর্যন্ত যে পরিচয়কে কেন্দ্র করে রাজনীতি গড়ে তোলা হয় সেই পরিচয়ের মানুষদেরই ভিক্টিম বানিয়ে ফেলে। সুতরাং নানান ঢং-এ ও নানান রঙ-এ পরিচয়বাদী রাজনীতিকে আমাদের বিরোধিতা করতে হবে। নোকতা হিসেবে বলা যায়, যতদিন পরিচয়কেন্দ্রীক শোষণ-শাসন ক্রিয়াশীল থাকবে ততদিন আবার পরিচয়ের রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি থেকে যাবে। এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে নিপীড়নের শিকার পরিচয়ের মানুষদের রেজিস্টেন্সকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমাদেরকে তাদের কাছাকাছি যেতে হবে এবং সংহতির মধ্য দিয়েই ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে হবে পরিচয়বাদী রাজনীতির ভয়াবহতা আসলে কতটা। এইদিকটা মনোযোগ না দিলে পরিচয়বাদী রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়াতে ডিলেমায় পরতে হতে পারে।
পরিশেষে শ্বাস নেয়ার লড়াইয়ে সকলকে মাঠের সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। লেখার শেষে লেখক সহ বইটি প্রকাশে যেসব শ্রমিক শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।