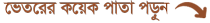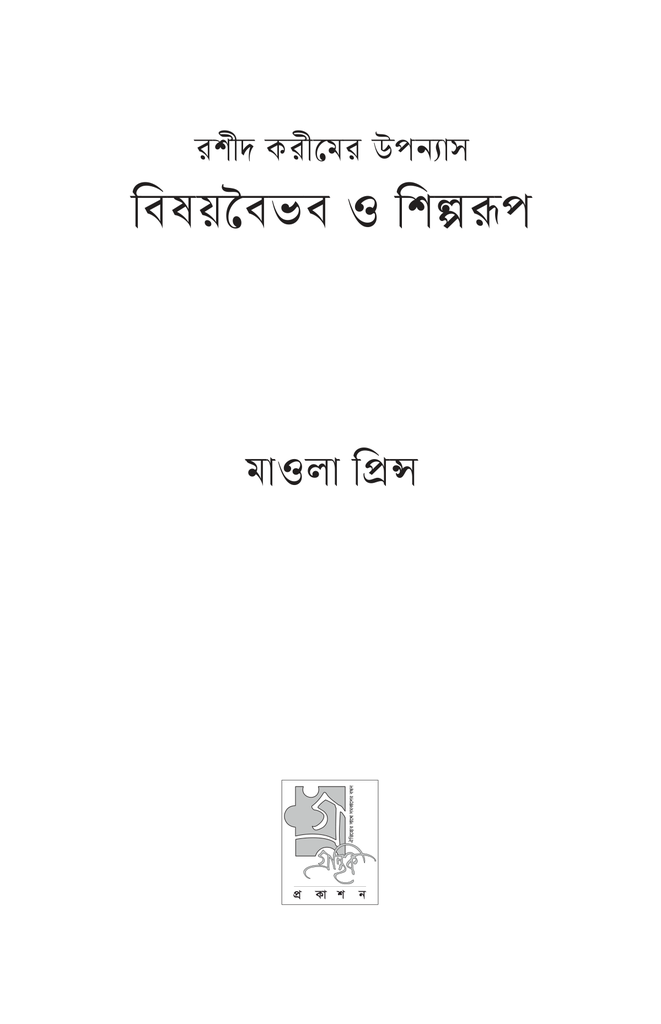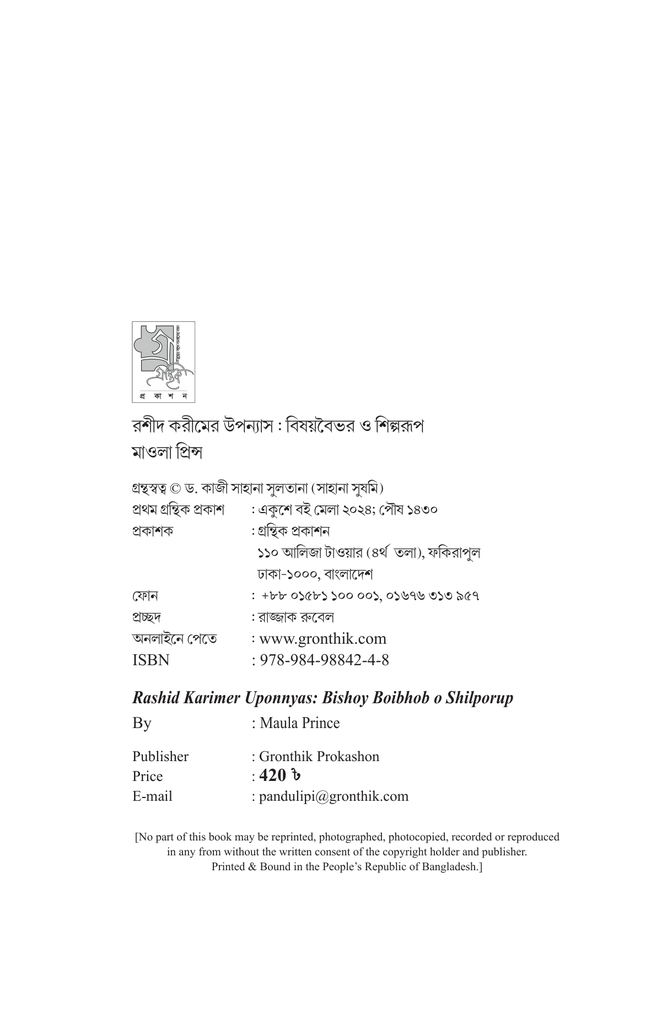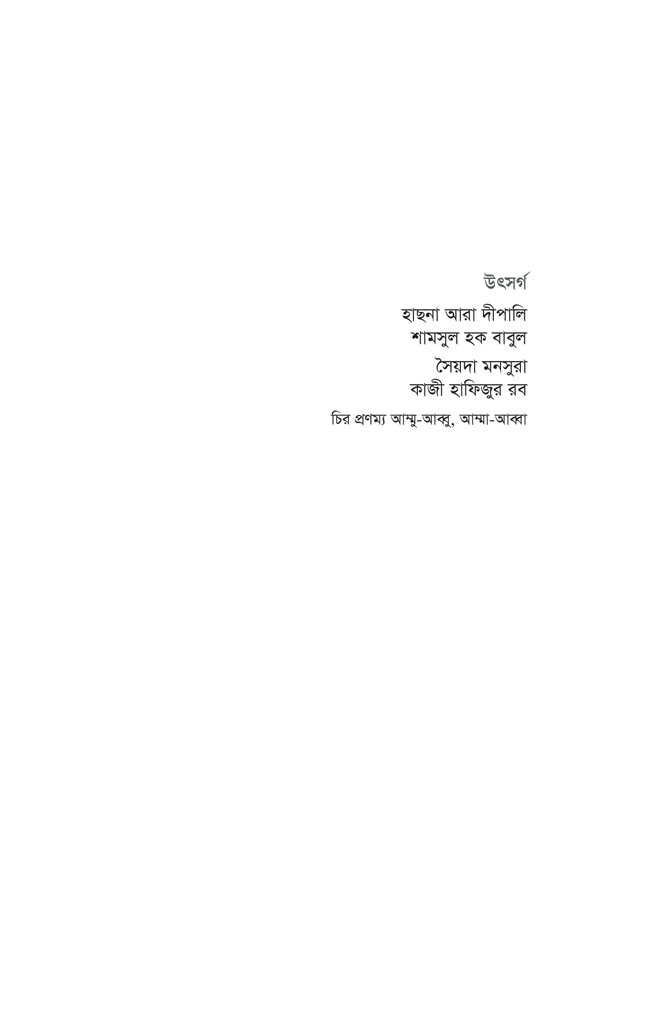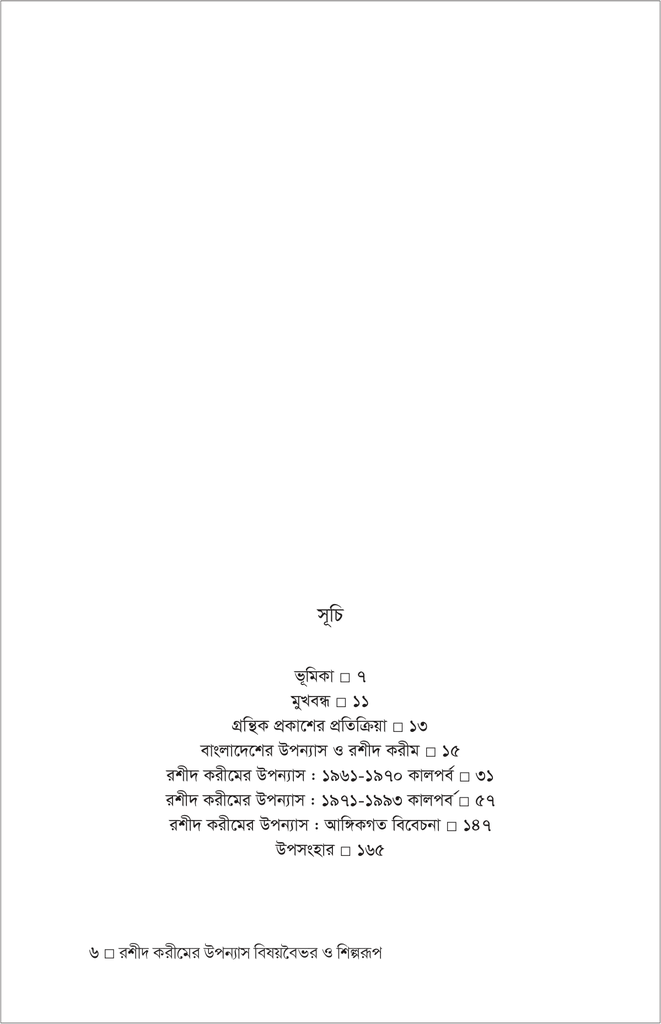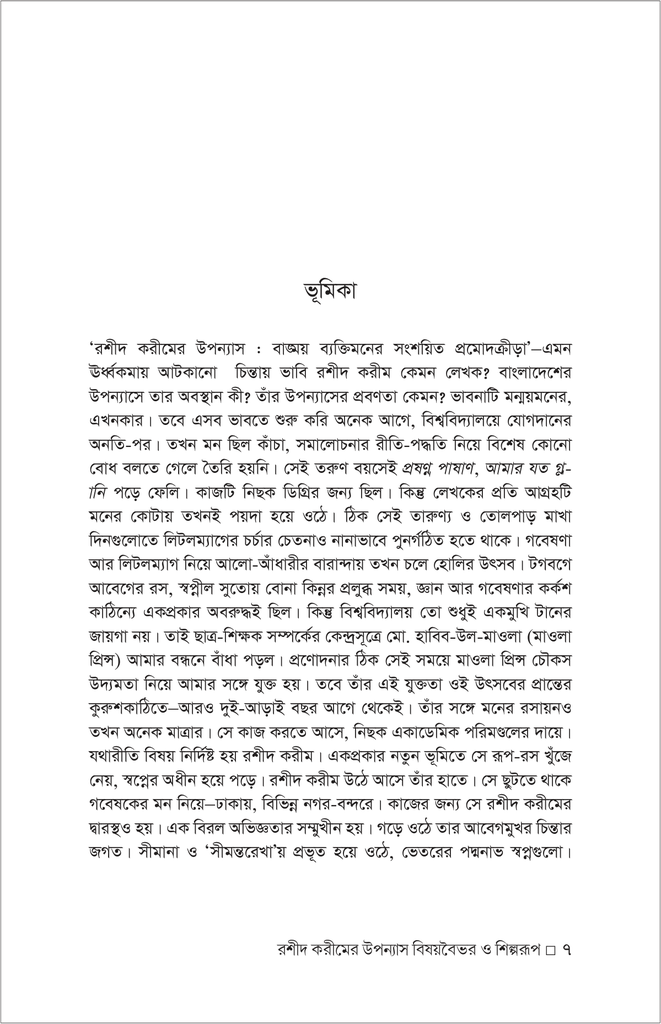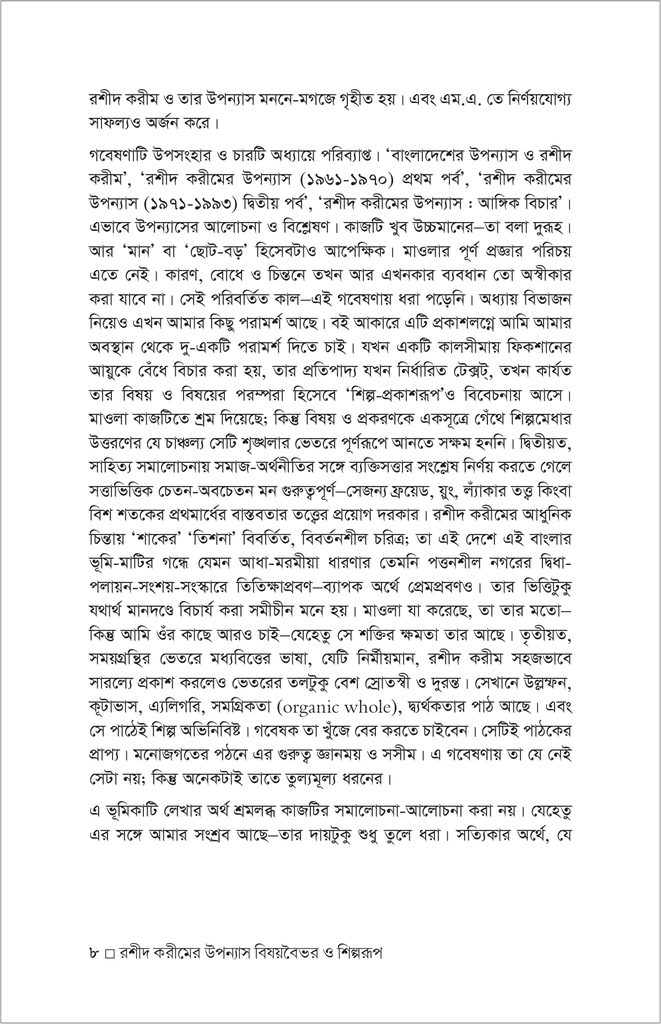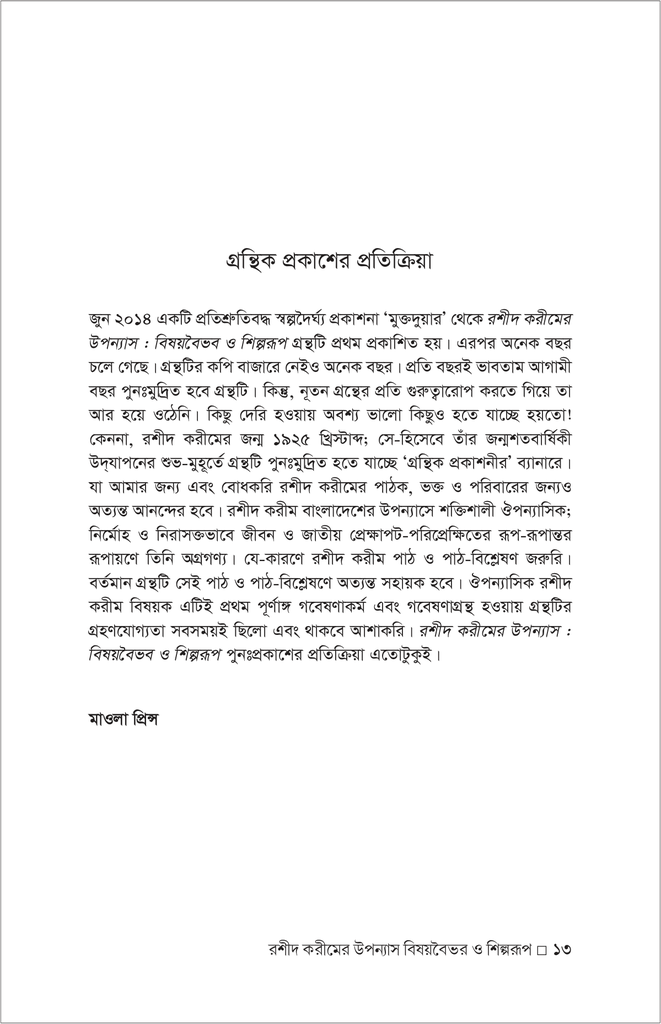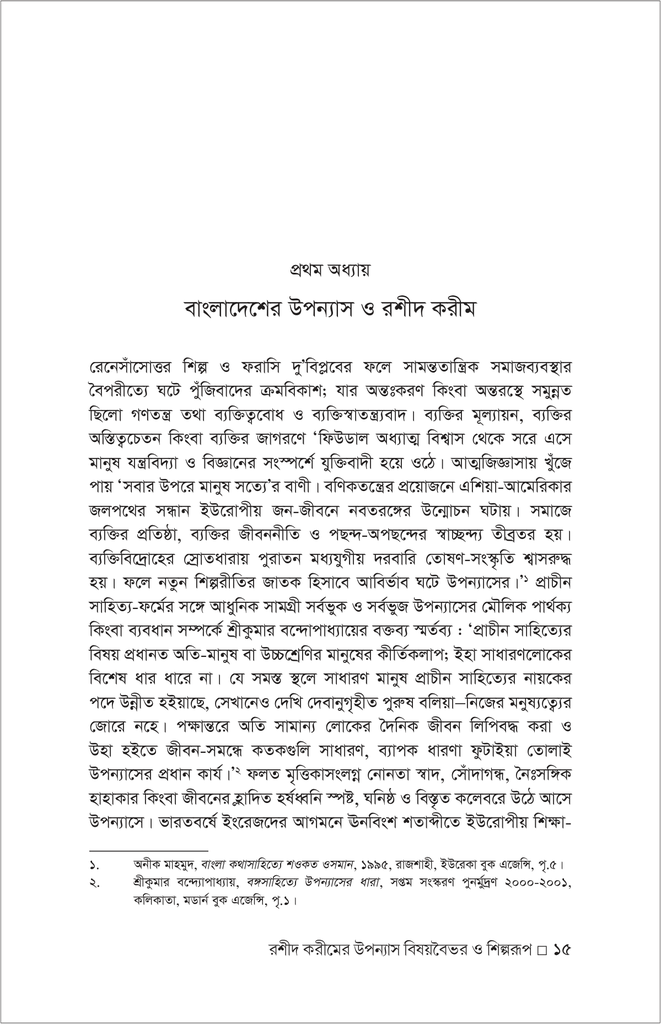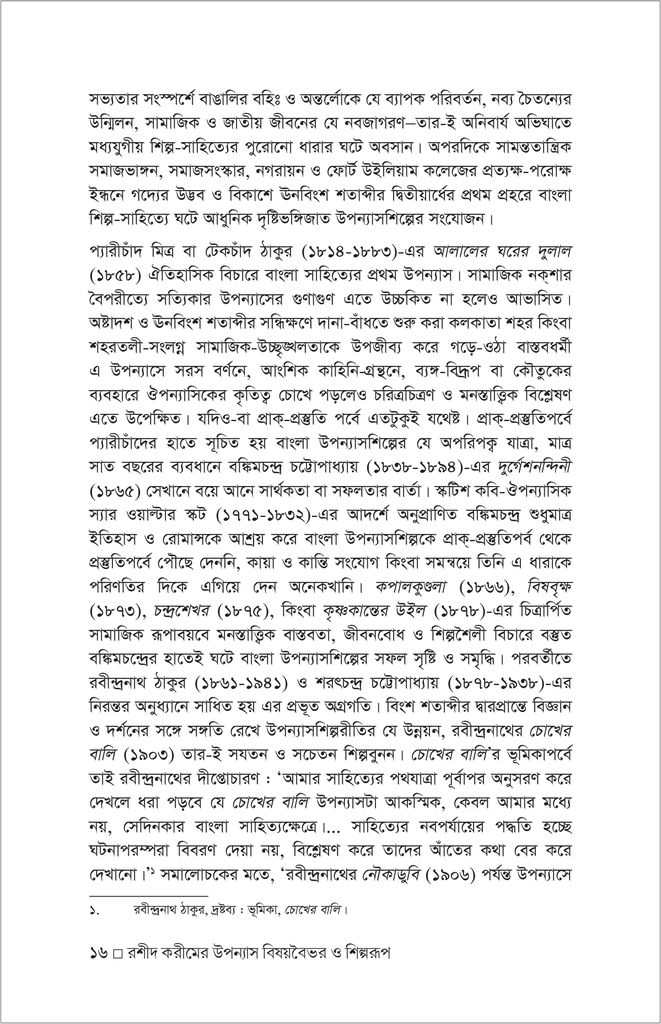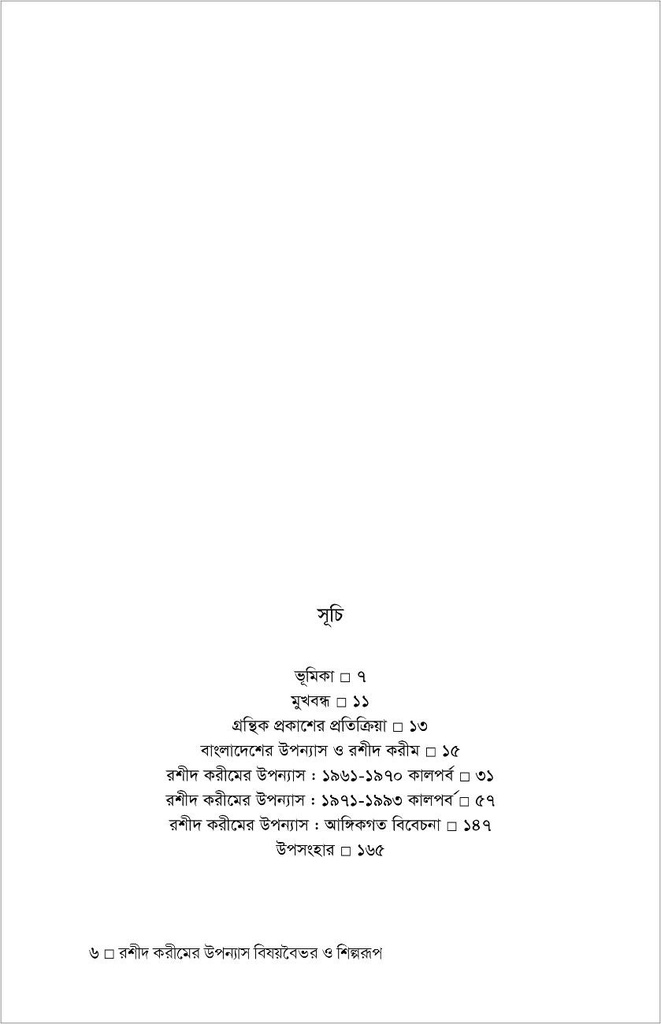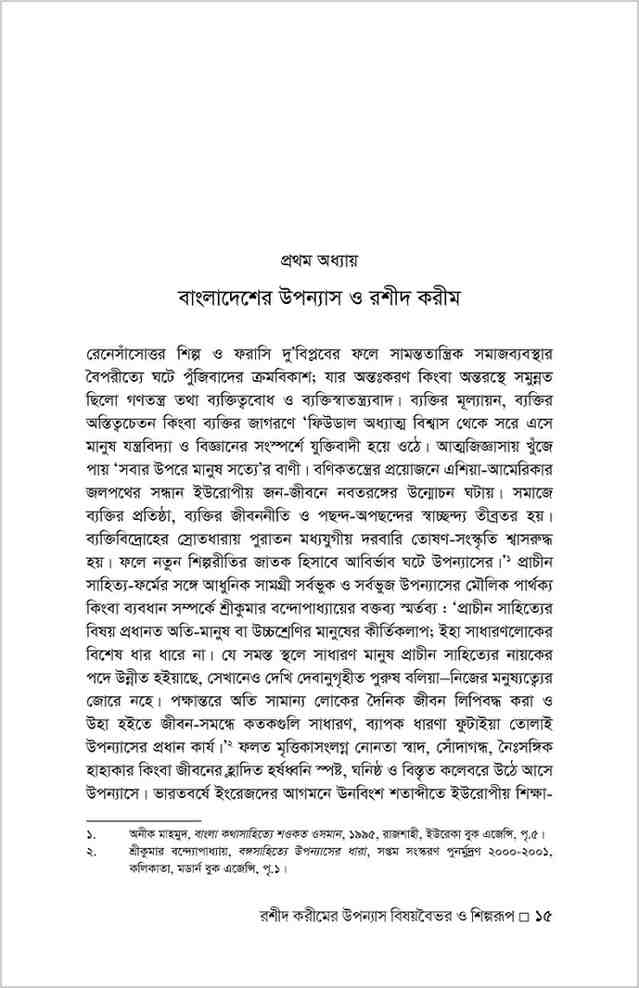রশীদ করীমের উপন্যাস : বাক্সময় ব্যক্তিমনের সংশয়িত প্রমোদক্রীড়া’-এমন ঊর্ধ্বকমায় আটকানো চিন্তায় ভাবি রশীদ করীম কেমন লেখক? বাংলাদেশের উপন্যাসে তার অবস্থান কী? তাঁর উপন্যাসের প্রবণতা কেমন? ভাবনাটি মন্ময়মনের, এখনকার। তবে এসব ভাবতে শুরু করি অনেক আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অনতি-পর।
তখন মন ছিল কাঁচা, সমালোচনার রীতি-পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ কোনো বোধ বলতে গেলে তৈরি হয়নি। সেই তরুণ বয়সেই প্রষণ্ড পাষাণ, আমার যত গ্লানি পড়ে ফেলি। কাজটি নিছক ডিগ্রির জন্য ছিল। কিন্তু লেখকের প্রতি আগ্রহটি মনের কোটায় তখনই পয়দা হয়ে ওঠে। ঠিক সেই তারুণ্য ও তোলপাড় মাখা দিনগুলোতে লিটলম্যাগের চর্চার চেতনাও নানাভাবে পুনর্গঠিত হতে থাকে। গবেষণা আর লিটলম্যাগ নিয়ে আলো-আঁধারীর বারান্দায় তখন চলে হোলির উৎসব।
টগবগে আবেগের রস, স্বপ্নীল সুতোয় বোনা কিন্নর প্রলুব্ধ সময়, জ্ঞান আর গবেষণার কর্কশ কাঠিন্যে একপ্রকার অবরুদ্ধই ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো শুধুই একমুখি টানের জায়গা নয়। তাই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কেন্দ্রসূত্রে মো. হাবিব-উল-মাওলা (মাওলা প্রিন্স) আমার বন্ধনে বাঁধা পড়ল। প্রণোদনার ঠিক সেই সময়ে মাওলা প্রিন্স চৌকস উদ্যমতা নিয়ে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে তাঁর এই যুক্ততা ওই উৎসবের প্রান্তের কুরুশকাঠিতে-আরও দুই-আড়াই বছর আগে থেকেই। তাঁর সঙ্গে মনের রসায়নও তখন অনেক মাত্রার। সে কাজ করতে আসে, নিছক একাডেমিক পরিমণ্ডলের দায়ে। যথারীতি বিষয় নির্দিষ্ট হয় রশীদ করীম। একপ্রকার নতুন ভূমিতে সে রূপ-রস খুঁজে নেয়, স্বপ্নের অধীন হয়ে পড়ে।
রশীদ করীম উঠে আসে তাঁর হাতে। সে ছুটতে থাকে গবেষকের মন নিয়ে-ঢাকায়, বিভিন্ন নগর-বন্দরে। কাজের জন্য সে রশীদ করীমের দ্বারস্থও হয়। এক বিরল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। গড়ে ওঠে তার আবেগমুখর চিন্তার জগত। সীমানা ও ‘সীমন্তরেখা’য় প্রভূত হয়ে ওঠে, ভেতরের পদ্মনাভ স্বপ্নগুলো। রশীদ করীম ও তার উপন্যাস মননে-মগজে গৃহীত হয়। এবং এম.এ. তে নির্ণয়যোগ্য সাফল্যও অর্জন করে। গবেষণাটি উপসংহার ও চারটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। ‘বাংলাদেশের উপন্যাস ও রশীদ করীম’, ‘রশীদ করীমের উপন্যাস (১৯৬১-১৯৭০) প্রথম পর্ব’, ‘রশীদ করীমের উপন্যাস (১৯৭১-১৯৯৩) দ্বিতীয় পর্ব’, ‘রশীদ করীমের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার’। এভাবে উপন্যাসের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। কাজটি খুব উচ্চমানের-তা বলা দুরূহ। আর ‘মান’ বা ‘ছোট-বড়’ হিসেবটাও আপেক্ষিক। মাওলার পূর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয় এতে নেই। কারণ, বোধে ও চিন্তনে তখন আর এখনকার ব্যবধান তো অস্বীকার করা যাবে না।
সেই পরিবর্তিত কাল-এই গবেষণায় ধরা পড়েনি। অধ্যায় বিভাজন নিয়েও এখন আমার কিছু পরামর্শ আছে। বই আকারে এটি প্রকাশলগ্নে আমি আমার অবস্থান থেকে দু-একটি পরামর্শ দিতে চাই। যখন একটি কালসীমায় ফিকশানের আয়ুকে বেঁধে বিচার করা হয়, তার প্রতিপাদ্য যখন নির্ধারিত টেক্সট্, তখন কার্যত তার বিষয় ও বিষয়ের পরম্পরা হিসেবে ‘শিল্প-প্রকাশরূপ’ও বিবেচনায় আসে। মাওলা কাজটিতে শ্রম দিয়েছে; কিন্তু বিষয় ও প্রকরণকে একসূত্রে গেঁথে শিল্পমেধার উত্তরণের যে চাঞ্চল্য সেটি শৃঙ্খলার ভেতরে পূর্ণরূপে আনতে সক্ষম হননি। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সমালোচনায় সমাজ-অর্থনীতির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সংশ্লেষ নির্ণয় করতে গেলে সত্তাভিত্তিক চেতন-অবচেতন মন গুরুত্বপূর্ণ-সেজন্য ফ্রয়েড, য়ুং, ল্যাঁকার তত্ত¡ কিংবা বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাস্তবতার তত্তে¡র প্রয়োগ দরকার। রশীদ করীমের আধুনিক চিন্তায় ‘শাকের’ ‘তিশনা’ বিবর্তিত, বিবর্তনশীল চরিত্র; তা এই দেশে এই বাংলার ভূমি-মাটির গন্ধে যেমন আধা-মরমীয়া ধারণার তেমনি পত্তনশীল নগরের দ্বিধা-পলায়ন-সংশয়-সংস্কারে তিতিক্ষাপ্রবণ-ব্যাপক অর্থে প্রেমপ্রবণও।
তার ভিত্তিটুকু যথার্থ মানদণ্ড বিচার্য করা সমীচীন মনে হয়। মাওলা যা করেছে, তা তার মতো- কিন্তু আমি ওঁর কাছে আরও চাই-যেহেতু সে শক্তির ক্ষমতা তার আছে। তৃতীয়ত, সময়গ্রন্থির ভেতরে মধ্যবিত্তের ভাষা, যেটি নির্মীয়মান, রশীদ করীম সহজভাবে সারল্যে প্রকাশ করলেও ভেতরের তলটুকু বেশ স্রোতস্বী ও দুরন্ত। সেখানে উল্লম্ফন, কূটাভাস, এ্যলিগরি, সমগ্রিকতা (organic whole), দ্ব্যর্থকতার পাঠ আছে। এবং সে পাঠেই শিল্প অভিনিবিষ্ট। গবেষক তা খুঁজে বের করতে চাইবেন। সেটিই পাঠকের প্রাপ্য।
মনোজগতের পঠনে এর গুরুত্ব জ্ঞানময় ও সসীম। এ গবেষণায় তা যে নেই সেটা নয়; কিন্তু অনেকটাই তাতে তুল্যমূল্য ধরনের। এ ভূমিকাটি লেখার অর্থ শ্রমলব্ধ কাজটির সমালোচনা-আলোচনা করা নয়। যেহেতু এর সঙ্গে আমার সংশ্রব আছে-তার দায়টুকু শুধু তুলে ধরা। সত্যিকার অর্থে, যে পরামর্শসমূহ এখন ভাবছি-তা আজ হতে দশবছর পূর্বে ভাববার অবকাশ তেমন ছিল না-সে সীমাবদ্ধতার জন্য শিক্ষক হিসেবে নিশ্চয়ই আমার দায় আছে। মাওলা কাজটির গ্রন্থরূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছে, তখন শুধু তাকেই কেন, আমার সীমাবদ্ধতাটুকুও এখানে সাক্ষ্য হিসেবে থাকা শোভন বলেই মনে করি। মাওলার জন্য চির-আশীর্বাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।