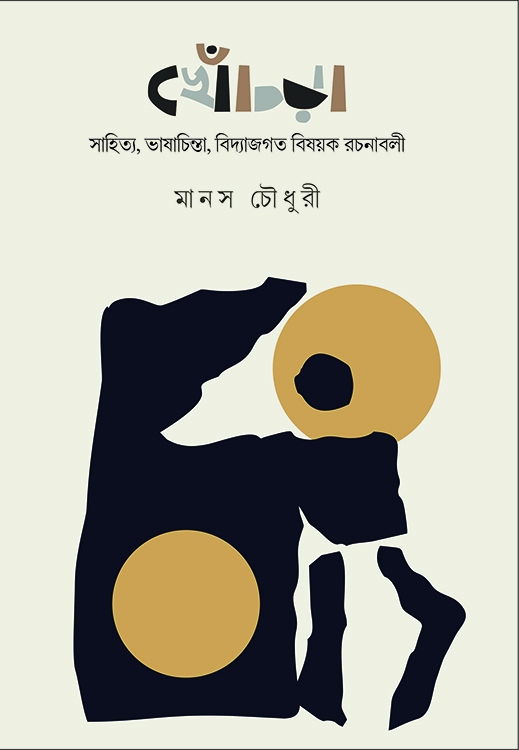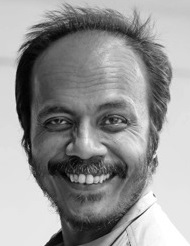লেখকের ভূমিকা হলো রচনা করা, প্রকাশকের ভূমিকা হচ্ছে সেসব রচনাকে প্রকাশ করা, আর পাঠকের ভূমিকা হলো সেসব পয়সা খরচ করে কিনে রাখা। তারপর ইচ্ছে হলে পড়া। এই রকম একটা চিত্র আমাদের মাথায় কাজ করে। কিন্তু জগত এত সহজ-সরল পথে চলে না। আর এরকম বন্দোবস্তের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম একটা কারসাজি আছে বলেও আমার মনে হয়। অন্তত আমি কারোরই কোনো ভূমিকা পূর্বনির্দিষ্ট রাখার পক্ষপাতী নই। তার মানে দাঁড়াল, যার যা খুশি তাই করবে। এমনকি অখুশি হয়েও করবে বা করে অখুশি হবে ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে প্রকাশনার একটা বড় অংশই মোটের উপর ‘যা খুশি তাই’ বটে।
রচনা আর প্রকাশনার মধ্যকার সেতুবন্ধটা মোটেই সহজ নয়। তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আছে। কিন্তু যখন যেখানেই সেই আলাপ করি না কেন, ঠিক এখানেই পুরো আলাপটা তুলতে চাইছি না। আপাতত যদি ধরেও নিই আগ্রহী প্রকাশকেরা লেখকদের ধরে-ধরে রচনা চান, তাতেও সেই ধরাধরির মধ্যে আমি খুব একটা বড় টার্গেট নই, ছিলাম না কখনো। তার থেকেও বড় কথা হলো, রচনা করার আলসেমির তুলনায় রচনা থেকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের আলসেমি আরও মহান ধরনের। ওটা প্রায় অসাধ্যসাধন মনে হয় আমার। রচয়িতার কাজ রচন, আর প্রকাশকের কাজ প্রকাশন হলে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নটা কার কাজ হবে? খুব নামীদামী লোক মরে গেলে তাঁদের রচনা থেকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে থাকেন অন্যান্য মানুষজন। ভক্তকুল, পরিবার-পরিজন, নেতা ধরনের কেউ হলে এবং মরণোত্তর কপাল বেশি মন্দ হলে এমনকি সংগঠনের ভাষাবিবর্জিত কর্মীবৃন্দ এসব কাজ করে থাকেন। জীবিতকালেও যে কারোই এই অভিজ্ঞতা হয় না তা নয়। ভাড়াইট্টা পদ্ধতিতে লোকজন বসিয়ে ‘বানায়া দে’ বলে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কিছু নমুনা আমি জানি। কিন্তু প্রমাণ দিতে পারব না। এই বর্গের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা, শিল্পপতি, এমনকি অধ্যাপক যে-কেউই থাকতে পারেন। অধ্যাপক বর্গ এমনকি চাইলে ‘পাণ্ডিত্যপূর্ণ’ কিতাবও এভাবে বানিয়ে ফেলতে পারেন। বাজারে অভিযোগ থাকে যে, কেউ কেউ এমনকি কোনোদিন নিজে রচেন নাই যাহা তাহাও পুস্তকাকারে বানিয়ে ফেলতে পারেন। এই আলাপে গ্রন্থের মধ্যকার সারবস্তু নিয়ে কথা হচ্ছে না, নিছকই পুস্তক নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। যাই হোক না কেন, কাজটা করা লাগে, এবং সেটা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ মনে হয় আমার। আর কাজটা আমি কাউকে দিয়ে করাইনি। ফলে মোটের উপর খুব উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান (ঘ্যানঘ্যানানিতে উত্তম যাঁরা) প্রকাশক ছাড়া ওই পর্যন্ত পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভবই হয় না।
ইংরেজি ‘আন্তর্জাতিক’ প্রকাশকবৃন্দ পুস্তকের চরিত্র বিষয়ে পাকাপাকি কতগুলো ধারণা বহন করেন। কোনটা মনোগ্রাফ, কোনটা এডিটেড ভল্যুম, কোনটা এসে-এনথোলজি এসব বিষয়ে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট তো বটেই, সেটা আমাদের প্রকাশকদেরও স্পষ্ট, কী তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন কিংবা কোনটা প্রকাশে অনীহ সেসব শক্তবিধিতে তাঁরা কার্য পরিচালনা করে থাকেন। সেখানে, যদি লক্ষ করে থাকেন, এসে-এনথোলজি বা রচনার সংকলন সবচেয়ে অনীহার মালামাল। লেখক খুব বিখ্যাত হলে (ও আরও ভাল হয় মৃত হলে) বিধিটা কিছু শিথিল হয় বটে। এই কথা তুললাম এই কারণে যে বাংলাদেশের প্রকাশকেরা এই ব্যাপারে মধুর সংযোগ। আর যাই হোক তাঁরা ‘মনোগ্রাফে’র জন্য জিদাজিদি করতে পারেন না। রচনা সংকলন প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ স্বর্গরাজ্য বিশেষ (বলেই মনে হয়)। নাহলে আমার খুব অসুবিধা হতো।
আমি যেহেতু প্রায় ২৫ বছর ধরে কম্প্যুটারে লিখি, এবং এই পঁচিশ বছরে মাত্র দেড় বছরের রচনাদি খোয়া-যাওয়া ছাড়া বড় কোনো ডেটা-বিপর্যয় নেই, আর ২৫ বছর আগের সামান্য রচনাদি নিয়ে আমার যেহেতু কোনো মায়া কাজ করে না, পাণ্ডুলিপি বানানো মোটের উপর আমার জন্য কম্প্যুটার খুলে ফোল্ডারে খোঁজাখুঁজি করতে-থাকা একটা কাজ দিয়ে শুরু হয়। কম্প্যুটারের ফোল্ডার অনেকটা রান্নাঘরের টিনের কৌটার মতো। রাখার সময় আপনার ঠিকই একদম পানির মতো স্পষ্ট মনে থাকবে ‘ওই যে সবুজ কৌটায় দারচিনি’ আর ‘বাদামি কৌটায় জিরা’, যখন রান্না করতে গেছেন তখন ১৭টা কৌটা খুলেও আর তেজপাতা বের করতে পারবেন না। এমনকি আপনার মনেও থাকবে না আদৌ তেজপাতা বাড়িতে রেখেছিলেন কিনা। ফলে, হতে পারে, আপনি কখনো রাখেননি যে তেজপাতা সেটাই হয়তো তিরিশটা কৌটা খুঁজে দেখে তারপর সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন ‘না নেই তাহলে’।
অন্য লেখকদের কথা আমি অবশ্যই জানি না, নিজের ক্ষেত্রে আমার এরকম হতেই থাকে। আমি নাম দিয়ে ফাইল বানানোর সময় ভাবি, সহজেই খুঁজে পাব; আর যখন খুঁজতে বসি, একটার পর একটা ফাইল না খুললে কিছুতেই নাম ধরে, ফোল্ডার ধরে সহজে কিছু খুঁজে পাই না। আবার কখনো লিখব বলে ভেবেছিলাম যে বিষয়ে সেই বিষয়ে আমার রচনা খুঁজতে থাকি ফোল্ডারের পর ফোল্ডার। খুঁজে খুঁজে ক্লান্তভাবে একসময় সিদ্ধান্তে আসি ‘তাহলে হয়তো লিখিনি, ভেবেছি যে লিখব’। এসব অশান্তি ডিঙিয়েই পাণ্ডুলিপি বানাতে হয় আমার। এবারেই তাই হলো। যা পেতে পারতাম এবং পাইনি সেসব বাদ দিয়ে যা আছে সেসব কম্প্যুটারে-থাকা রচনাকে কুড়িয়ে-কাছিয়ে জড়ো করে এই পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে।
একটা তাগড়া পাণ্ডুলিপি হতে পারত। এমনকি দুইটা বা তিনটা। মোটামুটি পঁচিশ বছর ধরে ভাষা-সাহিত্য-বিদ্যাজগত-প্রকাশনাচক্র নিয়ে আমি যা যা ভেবেছি তার সিকিভাগও যদি লেখা থাকত। হয়তো তখন এই মূলভাবগুলো আলাদা করেই পাণ্ডুলিপি বানাতে হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ অত লেখা হয়নি। যে কোনো নিন্দুকেই ভাবতে পারেন যে আমি চতুর্দিকে ছ্যাদরানো মনোযোগ দিই বলেই সাহিত্য নিয়ে আমার রচনা কম। সেটা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু এর থেকে বড় সত্য হলো আমি ৯০ ভাগ সময়ই লিখব-লিখব ভাব করতে থাকি, নিজেরই সাথে, তারপর লেখা হয় মাত্র ১০ ভাগ সময়। এত রকম দুর্যোগের পরও এই পাণ্ডুলিপিতে অনেক রচনাই রাখা গেল না।
রাখা গেল না যেসব রচনা সেগুলো যে মানের কারণে রাখা গেল না তা নয়। তাছাড়া নিজের লেখার মান খুব একটা আমি মাপতেও পারি না। ফলে সেটা বড় কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। খুঁজে পেয়েও না রাখতে পারা রচনাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত হতে পারিনি বলে বাদ দিয়েছি। এর মধ্যে বাদ দিতে গিয়ে সবচেয়ে মনোকষ্ট পেয়েছি কবিসভার রচনাগুলো নিয়ে। যাঁরা একদম জানেন না তাঁদেরকে জানানো দরকার যে কবিসভা বলে একটা ইমেইল-দল শুরু করেছিলেন ব্রাত্য রাইসু, ২০০৪ সালে। কমবেশি পাঁচশত লোকের একটা জমায়েত ছিল এই দল। এই দলটি পরিচালনও করতেন তিনি, তাঁর ভাষায় সঞ্চালন। ইয়াহুভিত্তিক এই ইমেইল-দলটিকে আমি বিবেচনা করি প্রাক-ব্লগ যুগের সর্বাধিক গুরুত্ববাহী সাহিত্যপ্রবাহ হিসেবে, এবং বাংলাদেশে ব্লগের প্রারম্ভিক দিকদর্শন হিসেবে। নানাবিধ কবিতা, গদ্য এবং কবিতালোচনা রাইসু নিজে ওয়ার্ড ফাইলে লেখকদের কাছ থেকে নিতেন এবং পিডিএফ করে তা সঞ্চালন করতেন। এই আমি কবি না হলেও সভাটির নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ছিলাম। এখানে ২০০৪ থেকে ২০০৭ সময়কালে আমি বিপুল পরিমাণ গদ্য রচনা করি। এর বড় একটা অংশ ছিল অন্যের কবিতা নিয়ে আলোচনা এবং নানাবিধ প্রবণতার ক্রিটিক। আমার ধারণা এই রচনার পরিমাণ ত্রিশ হাজার শব্দের অধিক। কিন্তু এই বইয়ে জায়গা দেবার জন্য সেসব আলোচনাকে যথেষ্ট প্রসঙ্গসূত্র দেয়া কঠিন বিশেষত অন্যের কবিতা নিয়ে আমার আলাপগুলোকে। একটা কারণ অবশ্যই এই যে সকলেই তারকা কবি ছিলেন না। কিন্তু সেটা মুখ্য কারণ নয়। এই বইতে অ-তারকা নিয়ে আলাপ আছে। বস্তুত, কবিসভার ইমেইল-দলের একটা গোষ্ঠীবদ্ধ বা বাউন্ড চরিত্র ছিল। সেটার বাইরে অনেক আলাপেরই ব্যঞ্জনালাঘব হয় বলে আমার মনে হয়েছে। ওগুলোর আর কোথাওই কখনো মুদ্রিত হওয়া হবে না সম্ভবত।
রচনাদির এই ‘বাউন্ড’ চরিত্রটি প্রায়শই তর্কালোচনায় উপেক্ষিত হয়। অনেকে রচনাকে এমন সার্বভৌম একটা ক্রিয়া ও উৎপাদ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন যেন বা সকল রচনাই ঈশ্বরের মতো নিরাকার ও নিঃলোকে উৎক্ষেপিত (বা ভূপাতিত)। আমি এই ধারণার ঘোরতর নিন্দুক। রচনা উৎসমূলেই দরবারের চরিত্র সাপেক্ষ। এমনকি কোথাও সেই দরবার ভৌতভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও রচয়িতা আপনি যেন বা জানেন কে আপনার রচনা পড়ছেন। এই যে পাঠককে জানা, বা যেন বা জানা, তা ছাড়া রচনাকে আমি দেখতে পাই না। রচনা এর সৃষ্টিকাল থেকেই, এমনকি তার আগে থেকেই, সম্পর্কবিচারে দ্বান্দ্বিক।
মানস চৌধুরী
আদাবর, ০৮ জানুয়ারি ২০২৫।